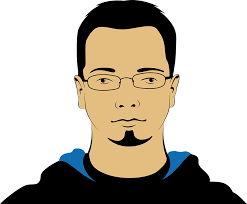

আজকাল আবহাওয়ার পূর্বাভাসে প্রায়ই এমন কিছু বৃষ্টির পূর্বাভাষ দেওয়া হয়, যা আগে দেখা যায়নি। এই ধরনের বৃষ্টিপাতের কারণে সৃষ্টি হওয়া বন্যাকে ‘শতবর্ষের বন্যা’ বা ‘পাঁচশো বছরের বন্যা’ হিসেবে বর্ণনা করা হয়।
কিন্তু এই শব্দগুলোর আসল অর্থ কী? বিজ্ঞানীরা কীভাবে একটি বন্যার তীব্রতা নির্ধারণ করেন এবং কেনই বা এই চরম আবহাওয়ার ঘটনাগুলো ক্রমশ বাড়ছে?
বিজ্ঞানীরা বন্যা পরিমাপের জন্য কিছু গাণিতিক পদ্ধতি ব্যবহার করেন, যা সাধারণ মানুষকে একটি বিশেষ বন্যার অস্বাভাবিকতা বুঝতে সাহায্য করে। এর মাধ্যমে এক বন্যার সঙ্গে অন্যটির তীব্রতা তুলনা করা যায়।
মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ (U.S. Geological Survey) অনুসারে, বিজ্ঞানীরা একটি নির্দিষ্ট মাত্রার বন্যা হওয়ার সম্ভাবনাকে শতকরা হারে প্রকাশ করেন। উদাহরণস্বরূপ, ‘পাঁচশো বছরের বন্যা’-এর অর্থ হলো, ঐ তীব্রতার বন্যা এক বছরে হওয়ার সম্ভাবনা ০.২%।
অর্থাৎ, ৫০০ বছরে একবার এমন বন্যা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
আরেকটি ধারণা হলো, একটি নির্দিষ্ট তীব্রতার ঘটনা কত ঘন ঘন ঘটবে, তার পূর্বাভাস দেওয়া। আবহাওয়াবিদরা একটি বন্যার পুনরাবৃত্তির গড় সময় (recurrence interval) বিশ্লেষণ করেন।
ধরা যাক, কোনো এলাকার জন্য একটি নির্দিষ্ট বন্যার পুনরাবৃত্তি সময় ২৫ বছর। তার মানে, ঐ ধরনের বন্যা সাধারণত ২৫ বছর পর পর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
তবে, বন্যা কত বছরে একবার হবে, তার চেয়ে একটি নির্দিষ্ট বছরে বন্যার শতকরা সম্ভাবনা জানানোর পদ্ধতিটি বেশি কার্যকর। কারণ, বিরল বন্যাও কয়েক বছরের ব্যবধানে আঘাত হানতে পারে।
বিষয়টি অনেকটা পাশা খেলার মতো, যেখানে পরপর দুবার একই সংখ্যা (যেমন: ছয়) আসার সম্ভাবনা খুবই কম, কিন্তু একেবারে অসম্ভব নয়।
বন্যার পূর্বাভাস দেওয়ার সময় আরেকটি শব্দ প্রায়ই শোনা যায়, সেটি হলো ‘আজীবনকালের ঘটনা’ অথবা ‘এক প্রজন্মের ঘটনা’। এর মাধ্যমে বোঝানো হয়, এই বন্যা হয়তো আগে দেখা যায়নি এবং অনেকের অভিজ্ঞতার বাইরে।
জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বন্যার ধরনেও পরিবর্তন আসছে। উদাহরণস্বরূপ, ২০১৫ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের হিউস্টন শহরে তিনবার ‘পাঁচশো বছরের বন্যা’ আঘাত হেনেছিল।
এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাতের রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছিল ঘূর্ণিঝড় হার্ভের সময়। ভয়াবহ বন্যায় ঘরবাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভেসে গিয়েছিল এবং বহু গাড়ি পানির স্রোতে তলিয়ে গিয়েছিল।
যদিও গণিত ব্যবহার করে বন্যার সম্ভাবনা পরিমাপ করা যায়, প্রকৃতির নিজস্ব নিয়ম রয়েছে। স্থানীয় আবহাওয়ার ধরন এবং এল নিনোর মতো বৃহৎ ঘটনাগুলো বন্যার সম্ভবনাকে প্রভাবিত করে।
বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে, যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেড়েছে এবং এর ফলে বন্যা একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, মানুষের দ্বারা নির্গত কার্বন ডাই অক্সাইড ও মিথেন গ্যাসের কারণে পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ছে, ফলে জলীয় বাষ্প ধারণের ক্ষমতাও বাড়ছে।
নর্দার্ন ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়ুমণ্ডলীয় বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ভিক্টর জেনসিনি বলেছেন, তাপমাত্রা প্রতি ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়লে, বায়ুমণ্ডল প্রায় ৭% বেশি জলীয় বাষ্প ধরে রাখতে পারে। এই জলীয় বাষ্পই বৃষ্টি বা তুষার আকারে ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসে।
তাঁর মতে, গত তিন দশকে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা বেড়েছে।
অন্যদিকে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে কিছু অঞ্চলে খরা দেখা যাচ্ছে। নাসা-র তথ্য অনুযায়ী, অতিবৃষ্টি এবং তীব্র খরা এখন আরও বেশি ঘটছে।
বিশ্বজুড়ে চরম আবহাওয়ার এই পরিস্থিতি, জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত।
তথ্য সূত্র: এসোসিয়েটেড প্রেস