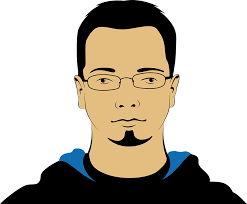

শিরোনাম: ছবি বনাম সত্যি: কীভাবে বিশ্বকে বোকা বানিয়েছে কিছু ভুয়া ছবি
ছবি, যা একবার চোখের সামনে দেখা গেলেই সত্য হিসেবে ধরে নেওয়া হতো, সেই ছবিই এখন মিথ্যার মোড়কে বন্দী। ক্যামেরার জন্মলগ্ন থেকে ছবি তোলার ধারণাটা মানুষের মনে গেঁথে গিয়েছিল— ক্যামেরাই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ।
কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই ধারণায় ফাটল ধরেছে। প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে বেড়েছে ছবি সম্পাদনার কারিকুরি, যা অনেক সময়েই আসলকে ছাপিয়ে যায়। আসুন, এমন কিছু ভুয়া ছবির গল্প শোনা যাক, যা দেখে বিশ্ববাসী বিভ্রান্ত হয়েছে।
শুরুতেই আসা যাক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের কথায়। তিনিই ছিলেন প্রথম প্রেসিডেন্ট, যিনি ক্যামেরাবন্দী হয়েছিলেন।
কিন্তু এখানেও ছিল কারসাজি। লিংকনের একটি প্রতিকৃতি তৈরি করতে তাঁর মুখের ছবি অন্য একজনের শরীরের ওপর বসানো হয়েছিল, যা সম্ভবত প্রচারের একটি কৌশল ছিল। একইভাবে, গৃহযুদ্ধের জেনারেল ইউলিসিস এস গ্রান্টের ছবিতেও তিনটি আলাদা দৃশ্যের সমন্বয় ঘটানো হয়েছিল, যাতে তাঁকে আরও শক্তিশালী ও প্রভাবশালী দেখানো যায়।
রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ছবি ব্যবহারের বিষয়টি বেশ পুরোনো। প্রতিপক্ষকে ছোট করতে অথবা নিজেদের ভালো প্রমাণ করতে প্রায়ই ছবিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।
উদাহরণস্বরূপ, উত্তর কোরিয়া তাদের সামরিক শক্তি বাড়াতে অতিরিক্ত যুদ্ধজাহাজের ছবি ব্যবহার করেছে, যা তাদের আরও শক্তিশালী হিসেবে তুলে ধরেছে। আবার, ২০০৪ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় রিপাবলিকানরা ডেমোক্রেটদের বিরুদ্ধে জন কেরিকে ভিয়েতনাম যুদ্ধের সমালোচক ‘হানোই জেন’-এর সঙ্গে যুক্ত করে ছবি প্রকাশ করে, যা ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা।
রাজনীতির বাইরেও, খ্যাতি লাভের উদ্দেশ্যে ছবি সম্পাদনার ঘটনা ঘটেছে। যেমন, বিখ্যাত আলোকচিত্রী রবার্ট ক্যাপার তোলা একটি ছবিতে সৈনিকের মৃত্যুর দৃশ্য নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল।
অনেকের মতে, ছবিটি সাজানো ছিল। এছাড়া, অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যেও অনেক ভুয়া ছবি তৈরি হয়েছে, যেমন—বিগফুট-এর (এক প্রকার অতিকায় মানব) ছবি।
তবে কিছু ছবি আছে, যা কোনো সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য ছাড়াই তৈরি করা হয়েছে। যেমন, ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলার পর টুইন টাওয়ারের ছাদে এক ব্যক্তির ছবি, যা আসলে ছিল একটি নিছক কৌতুক।
এবার আসা যাক, বহুল আলোচিত কিছু ছবির প্রসঙ্গে:
ছবি সম্পাদনার এই খেলা নতুন নয়। প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এর কৌশল বেড়েছে, যা সাধারণ মানুষের পক্ষে আসল ও ভুয়া ছবির মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন করে তুলেছে।
তাই, ছবি দেখার সময় আমাদের আরও সতর্ক থাকতে হবে।
তথ্যসূত্র: দ্য গার্ডিয়ান